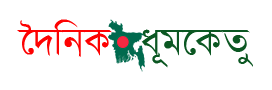বাংলাদেশে বসবাসরত ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাপনে যেমন রয়েছে বৈচিত্র্য, তেমনি রয়েছে স্বকীয়তা। তাদের উৎসব, ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা প্রভৃতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখছেন ধূমকেতু ডটকম-এর বিশেষ প্রতিবেদক নিখিল মানখিন। প্রকাশিত হচ্ছে প্রতি শনিবার। আজ প্রকাশিত হলো [৯ম পর্ব]। চোখ রাখুন ধূমকেতু ডটকম-এ।
নিখিল মানখিন, ধূমকেতু ডটকম: বাংলাদেশে বসবাসরত ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম। তারা ভারতীয় উপমহাদেশের এক প্রাচীন জাতি। বাংলাদেশ ও ভারতের ত্রিপুরাসহ কয়েকটি রাজ্যে বিপুল সংখ্যক ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বসবাস। এ জাতির রয়েছে সমৃদ্ধ ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ধর্ম বিশ্বাসে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সনাতন ধর্মের অনুসারী। বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসরত ত্রিপুরাদের কিছু অংশ খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তাদের প্রধান সামাজিক উৎসবের নাম ‘বৈসু’। ত্রিপুরাদের মাঝে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান। তাদের প্রধান জীবিকা কৃষি।
কাপেং ফাউন্ডেশনের গ্রোগ্রাম ম্যানেজার উজ্জ্বল আজিম ধূমকেতু ডটকমকে জানান, পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমাদের পরেই ত্রিপুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা ব্যাতীত ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সমতল এলাকার কুমিল্লা, সিলেট, বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা, রাজবাড়ি, চাঁদপুর, ফরিদপুর ইত্যাদি অঞ্চলে বর্তমানে বসবাস করে।
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বসবাস হলেও এ জাতির মূল অংশ বসবাস করছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়াও ভারতের মিজোরাম, আসাম প্রভৃতি প্রদেশেও বেশ উল্লেখযোগ্য ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বসতি দেখা যায়।
পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারেও ত্রিপুরাদের জনবসতি আছে। এককালে এই জাতি ভারতবর্ষে এক পরাক্রমশালী জাতি হিসেবে স্বাধীন সার্বভৌম ত্রিপুরা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।
জনসংখ্যা ও ভাষা:
আদিবাসী নারী নেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা জানান, ত্রিপুরা জাতির ভাষার নাম ককবরক। ‘কক’ মানে ‘ভাষা’। ‘বরক’ মানে ‘মানুষ’। ‘ককবরক’ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ‘মানুষের ভাষা’। এ ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। ককবরক ভাষায় দু’ধরনের লিপিতে লেখার প্রচলন রয়েছে- রোমান ও বাংলা। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী প্রায় ১৪ লক্ষাধিক ত্রিপুরা ককবরক ভাষায় কথা বলে।
মধ্যযুগে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী-শাষিত পূর্ববঙ্গের এক বিশাল এলাকায় ককবরক প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরা জাতি মোট ৩৬টি দফায় বা গোত্রে বিভক্ত। বাংলাদেশে ১৬টি গোত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের মধ্যে উপভাষা-ভেদ রয়েছে। অনেক আগে থেকেই ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ককবরক ভাষা বাংলা হরফে লিখিত হয়ে আসছে। ককবরকের ব্যাকরণ অনেক পুরনো।
১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে ত্রিপুরা জনসংখ্যা ৮১,০১৪ জন। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ত্রিপুরা জনসংখ্যা ১,১৯,৯০১ জন। বর্তমানে ত্রিপুরাদের জনসংখ্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে দেড় লাখের বেশি। এছাড়া ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ১২ লাখ, মিজোরামে ১ লাখ ২০ হাজার এবং আসামে ৩০ হাজার ত্রিপুরা জনসংখ্যা রয়েছে বলে জানা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে ত্রিপুরাদের জনসংখ্যা দুই লাখের কাছাকাছি হবে ত্রিপুরা নেতৃবৃন্দের দাবি।
বিবাহ:
আদিবাসী নেতা সন্তোষ কুমার ত্রিপুরা বলেন, ত্রিপুরা সমাজব্যবস্থায় চার ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় । এগুলি হলো – হামজাকলাই লামা, খকয়ৈই লামা, ফারান খৗলায়ৈ লামা ও চামিরি কামা।
উভয়পক্ষের অভিভাবক এবং ভাবী বর-কনের সম্মতিক্রমে সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়া বিয়েকে হামজাক-লাই লামা বিবাহ বলে।
আর কোনো একটি অভিভাবক পক্ষ বা উভয় অভিভাবক পক্ষের সম্মতি ছাড়া শুধু বর-কনের সম্মতিক্রমে হওয়া বিয়ের নাম ‘খকয়ৈ লামা’। এ ধরনের বিয়েতে যদি বর পক্ষের অভিভাবকের মতামত থাকে সে ক্ষেত্রে কনের বাড়িতেই সামাজিকভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে।
বর-কনে ও উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতিতে সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে কনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিয়ের নাম ‘চামিরি কামা’। এই বিয়ের মাধ্যমে বর কনের বাড়িতে যায় এবং কনের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। যে সব চামিরি বা বর এর আর্থিক অবস্থা ভালো না, সাধারণত তারাই কনের বাড়িতে বর হিসেবে উঠে যায়।
আর পরিবারে ছেলে সন্তান না থাকলে সেই পরিবারের অভিভাবকরা মেয়ের জন্য পছন্দসই বর পেলে জামাইকে নিয়ে আসে নিজের বাড়িতে। এটাকেই ত্রিপুরা সমাজে ‘চামিরি কামা’ বলে।
খাদ্য:
নারী নেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা বলেন, ত্রিপুরাদের খাদ্য তালিকায় বাঙালি খাদ্য অনেক আগেই অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। তবে কিছুক্ষেত্রে তারা এখনও বিশেষ খাদ্য ও রান্নায় নিজস্ব বিশেষ প্রক্রিয়া ধরে রেখেছে।
ত্রিপুরাদের প্রধান খাদ্য ভাত। ভাতের সঙ্গে থাকে সিদ্ধ সবজি, মরিচ ও ভুট্টা। তাদের শাক-সবজি সিদ্ধ মানেই মরিচ ও ভুট্টার উপস্থিতি। তারা বাঁশ কোড়লকে চাখৈ, মৈতুরু, বাংসোং, কেসক, লাকসু, বাজি প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে খেয়ে থাকে। সবজি হিসেবে ঢেড়স, কলাগাছ, মাশরুম, ঝিঙ্গা, হলুদ ফুল, আদা ফুলকে তারা সিদ্ধ এবং গুদাক (বিশেষ এক প্রক্রিয়া) করে খায়। ত্রিপুরারা মাছকে রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়ে খেতে পছন্দ করে।
ত্রিপুরাদের মাংস রান্নাকে সুস্বাদু করতে একরকম বিশেষ সুগন্ধি পাতা ‘বানা’ দেয়া হয়। বিন্নিচাল, কলাপাতা এবং লাইরু পাতা দিয়ে তারা পিঠা তৈরি করে থাকে। অতিথি আপ্যায়নে ত্রিপুরাদের রয়েছে বিশেষ সুখ্যাতি।
ধর্ম:
আদিবাসী নেত্রী চৈতালী ত্রিপুরা বলেন, ত্রিপুরারা মূলত সনাতন (হিন্দু ধর্ম) ধর্মাবলম্বী। তবে বর্তমানে বান্দরবান জেলার ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ এবং খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায়ও ত্রিপুরাদের একটি অংশ বর্তমানে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। সনাতন ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকেরা দুর্গা পূজা, কালী পূজা, রাসমেলা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে।
অপরদিকে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বড়দিন পালন করে। সারা বাংলাদেশে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বী আনুমানিক ৮০ শতাংশ এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ২০ শতাংশ হতে পারে।
সামাজিক উৎসব:
সন্তোষ কুমার ত্রিপুরা বলেন, ত্রিপুরাদের প্রধান সামাজিক উৎসবের নাম ‘বৈসু’। তারা তিনদিন ধরে এই সব উদযাপন করে থাকে। এগুলো হলো -হারি বৈসু, বৈসুমা ও বিসিকাতাল। পুরনো বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোকে কেন্দ্র করে এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব উদযাপন করা হয়ে থাকে।
এই তিন দিনে বিন্নি চাল দিয়ে নানা ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। নারী পুরুষেরা নতুন নতুন কাপড়-চোপড় পরিধান করে আনন্দে মেতে উঠে।এদিনে গান-বাজনা হয়, খেলাধুলা হয়। বৈসু উপলক্ষে ৫/৭ দিন ধরে ‘গড়িয়া নৃত্য’ পরিবেশন করা হয়। দল বেঁধে গড়িয়া দল গ্রামে গ্রামে ঘুরে গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করে।
বৈসুমার দিনে ধনী-গরিব সবাই সামর্থ্যানুযায়ী নানা ধরনের পিঠা, মদ, সরবত, পাঁচন ইত্যাদি অতিথিদের পরিবেশন করে। তবে ‘বৈসুমা’র দিনে প্রাণীবধ একেবারেই নিষিদ্ধ। ‘বৈসুমা’র দিনেও গড়িয়া নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এছাড়া পালা গান ও বিভিন্ন খেলাধুলা সারাদিন ধরে চলে।
এদিকে নতুন বছরে সুন্দর ও নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশায় সমাজের সকল বয়সের মানুষ বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। বিশেষ করে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীরা নতুন কাপড়-চোপড় পরিধান করে গ্রামের ঘরে ঘরে হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য পশু-পাখির খাবার বিলিয়ে দেয় এবং ত্রিপুরা সামাজিক রীতি অনুসারে বয়স্কদের পা ধরে সালাম করে আর্শীবাদ গ্রহণ করে।
এদিনে পরিবারের সকল সদস্যের মঙ্গলের জন্য পূজা ও উপাসনা করা হয়।
সামাজিক রীতিনীতি:
পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর আদিবাসীদের ন্যায় ত্রিপুরা জাতিরও ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব প্রথা, রীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। এ জনগোষ্ঠীর ভূমি মালিকানার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অলিখিত। যে ব্যক্তি কোনো বন পাহাড়কে প্রথম একবার জুমচাষ বা ভোগদখল করবে, সেদিন থেকেই সেই জুমভূমি তার হবে। মালিক বা প্রথম ভোগদখলকারী ব্যক্তির অনুমতি ব্যতিত এই জুমভূমি অন্য কেউ ভোগদখল বা চাষ করতে পারবে না।
প্রথম দখলের মধ্য দিয়ে মালিকানা নির্ধারিত হয়ে যায়। বিষয়টি গ্রামপ্রধান ‘কার্বারী’ ও গ্রামবাসীর জানা থাকলেই হলো। ভূমি মালিকানার বিষয়ে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রীতি অনুসারে লিখিত ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই। গ্রামবাসীরা গ্রামপ্রধান বা কার্বারীর নেতৃত্বে গ্রাম এলাকার বনকে এক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করে থাকেন। গ্রাম এলাকার বনকে তারা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে থাকেন। যেমন: জুমভূমি, গো চারণভূমি ও রিজার্ভ বা কালিত্র। জুমভূমি হলো জুমিয়াদের জুম চাষের জন্য, গো চারণভূমি হলো গরু-মহিষ চরানোর জন্য এবং রিজার্ভ বা কালিত্র হলো কার্বারী বা হেডম্যান-এর নেতৃত্বে গৃহ নির্মাণের জন্য বাঁশ-গাছের জন্য সংরক্ষিত এলাকা।
অর্থনেতিক অবস্থা ও পেশা:
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, ত্রিপুরাদের প্রধান পেশা কৃষি। তাছাড়া আছে চাকরিজীবী, কিছু ব্যবসায়ী ও দিনমজুর। সমাজে আর একটি পেশাজীবী আছে যারা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তারা জঙ্গল থেকে লাকড়ি, শন, তরকারি ইত্যাদি সংগ্রহ করে বিক্রি করে জীবনধারণ করে।
জুম চাষ ত্রিপুরাদের জীবন-জীবিকার প্রধান পেশা। সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ত্রিপুরা আদিবাসীরা অতীতে মূলত জুম চাষের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। জুমের উপর ভিত্তি করেই ত্রিপুরাদের অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ত্রিপুরাদের নাচ, গান, ছড়া, গল্প, মূল্যবোধ, বাদ্য-যন্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে জুম চাষকে কেন্দ্র করে।
নিজেদের চিরায়ত ভূমি হাতছাড়া হয়ে ত্রিপুরারা ভূমিহীন হয়ে পড়ছে। ফলে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ব্যবসা করে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম। এ জনগোষ্ঠীর কিছু কিছু লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করার চেষ্টা করছে। মুদি দোকান, মনোহারী দোকান, ঠিকাদারি, বনজ দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি ক্ষেত্রে ত্রিপুরাদের ব্যবসায করতে দেখা যায়। শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত বেকার লোকেরাই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকছে।
তবে পুঁজির স্বল্পতা, অঞ্চলের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সহজ-সরল উৎপাদন মানসিকতা, ব্যাংক ঋণের অভাব, প্রশাসনের অসহযোগিতা ইত্যাদি কারণে ত্রিপুরা ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় তেমন সুবিধা করতে পারছে না।
শিক্ষিত ত্রিপুরাদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকরি গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরাদের মধ্য থেকে হাতেগোনা কয়েকজন সরকারের বিসিএস ক্যাডারভুক্ত চাকরিজীবী রয়েছেন।
আরো পড়ুন:
মণিপুরীদের বিয়েতে আছে নানা বৈচিত্র্য | সমাজে নেই কোনো ভিক্ষুক